ওয়েবসাইট হলো পরস্পর সংযুক্ত কতগুলো ওয়েবপেজের সমষ্টি, যেখানে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট যেমন- টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন ইত্যাদি থাকে, যা কোনো ডোমেইনের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভারে হোস্টিং করা থাকে এবং যে-কেউ তা দেখতে পায়। ওয়েবসাইটের প্রথম পেজকে হোমপেজ বলে এবং প্রতিটি পেজকে ওয়েবপেজ বলে। যেমন- www.google.com, www.facebook.com, diploma.icu ইত্যাদি।
ওয়েব টেকনোলজি
ওয়েব টেকনোলজি বলতে এমন একটি টেকনোলজিকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মাল্টিমিডিয়া প্যাকেজগুলোকে ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। এটি মূলত হোস্ট করা ওয়েবসাইটের তথ্যগুলোর সাথে যোগাযোগ করার একটি উপায়।
ওয়েবপেজ অ্যাক্সেস করতে একটি ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করা হয়। ওয়েব ব্রাউজারগুলোর লাইব্রেরিতে এমন প্রোগ্রাম সেট করা থাকে, যাতে ওয়েবপেজে যুক্ত করা ডাটা, ছবি, অ্যানিমেশন এবং ভিডিও প্রদর্শন করতে পারে। ব্যবহারকারী ও ইন্টারনেট জগতের মধ্যে সমন্বয়সাদন করাই ব্রাউজারের কাজ। বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজার রয়েছে। যেমন- Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ইত্যাদি।
ওয়েব টেকনোলজিকে নিম্নলিখিত বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে-
১। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) : বিভিন্ন টেকনোলজির উপর ভিত্তি করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তৈরি করা হয়, যেমন- হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ (HTML), হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (HTTP)।
২। ওয়েব ব্রাউজারঃ ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার, যা সার্ভার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে যোগাযোগের উপায় তৈরি করে দেয়।
৩। ওয়েব সার্ভার: ওয়েব সার্ভার হলো এমন এক ধরনের সার্ভার, যা ওয়েবসাইটের কনটেন্ট জমা রাখে এবং যাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কোনো কম্পিউটার থেকে অ্যাক্সেস করা যায়। সার্ভারের সাথে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের যোগাযোগের জন্য হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (HTTP) ব্যবহার করা হয়।
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট: ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হলো ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা। অর্থাৎ, স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটকে ডায়নামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর করাই হলো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট-এর ক্ষেত্রে ডাটাবেস থাকা বাধ্যতামূলক। কেননা সকল তথ্য ডাটাবেসে জমা থাকে। ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োজন।
ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড এবং ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার
ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার(Front-end web)

ফ্রন্ট এন্ড হলো কোনো ওয়েবসাইটের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বা যে অংশটি ব্যবহারকারী দেখতে পায়। ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে HTML, সিএসএস (CSS), জাভাস্ক্রিপ্ট (JavaScript) ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে কোনো ওয়েবসাইটের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ডেভেলপ করা।
ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার জন্য সর্বপ্রথম ফ্রন্ট এন্ড তৈরি করতে হয়। কোনো ওয়েবসাইটের ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ দেখতে কেমন হবে, কোন কোন কালার ব্যবহৃত হবে, ছবি কোথায় বসবে বা বাটন কেমন হবে ইত্যাদি সবকিছুই ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের অংশ।
যে ব্যক্তি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপ করে, তাকে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার (Front-end web) বলে। একজন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপারের দক্ষতাগুলো নিচে দেয়া হলো-
- ওয়েবসাইটের বাহ্যিক অংশ বা ক্লায়েন্ট সাইড সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা।
- UI (User Interface) এবং UX (User Experience) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা।
- ওয়েবসাইটটি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে, যাতে গ্রাহকের চাহিদা পূরণ হয়।
- সবসময় নতুনত্ব বা মার্কেটের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থেকে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা।
- ওয়েবসাইটকে ইউজার ফ্রেন্ডলি বানানো।
- HTML, CSS, JavaScript সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (SEO) সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা।
- Responsive website তৈরি করা।
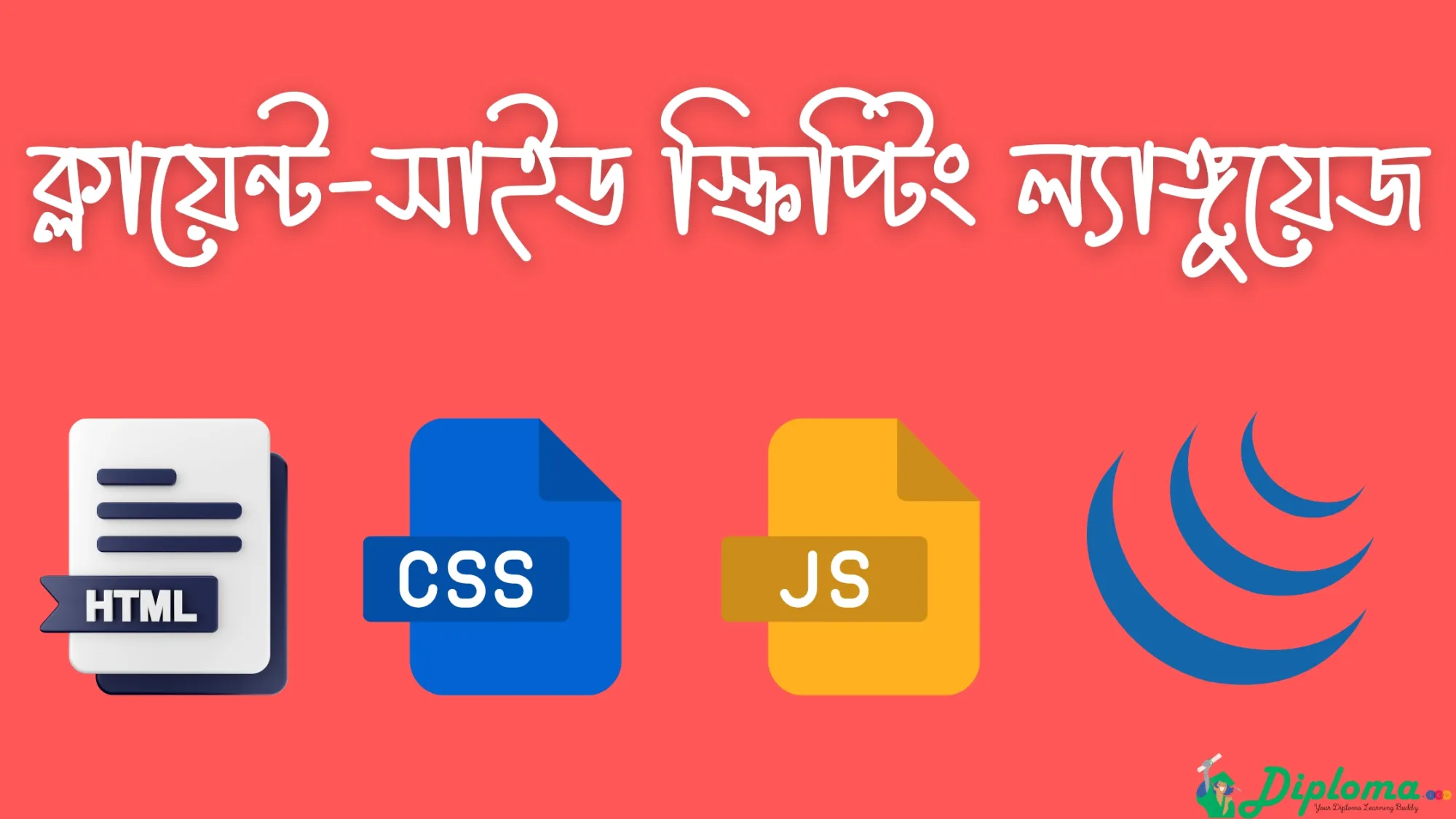
ব্যাক এন্ড ডেভেলপার(Back-end web)

ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট হলো ওয়েবসাইটের ভিতরের অদৃশ্যমান বিষয় বা সার্ভার নিয়ে কাজ করা। স্ট্যাটিক ওয়েবপেজ বা User interface-কে ডায়নামিক ওয়েবপেজে রূপান্তর করাই হলো ব্যাক এন্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। যে ওয়েব ডেভেলপার স্ট্যাটিক ওয়েবপেজকে ডায়নামিক ওয়েবপেজে রূপান্তর করে, তাকে ব্যাক এন্ড ওয়েব ডেভেলপার বলে।
ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা:
- ডায়নামিক ওয়েবপেজ তৈরির কলাকৌশল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
- সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন- (PHP/Python/ASP.NET) ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
- রিলেশনাল ডাটাবেস সম্পর্কে দক্ষতা থাকতে হবে, যেমন- SQL/NoSQL (MySQL/MongoDB)।
ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার(Full Stack Developer):
যে ব্যক্তি ফ্রন্ট এন্ড ও ব্যাক এন্ড উভয় ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে পারে, তাকে ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার বলে।
একজন ওয়েব ডেভেলপারের ভূমিকা/দায়িত্ব
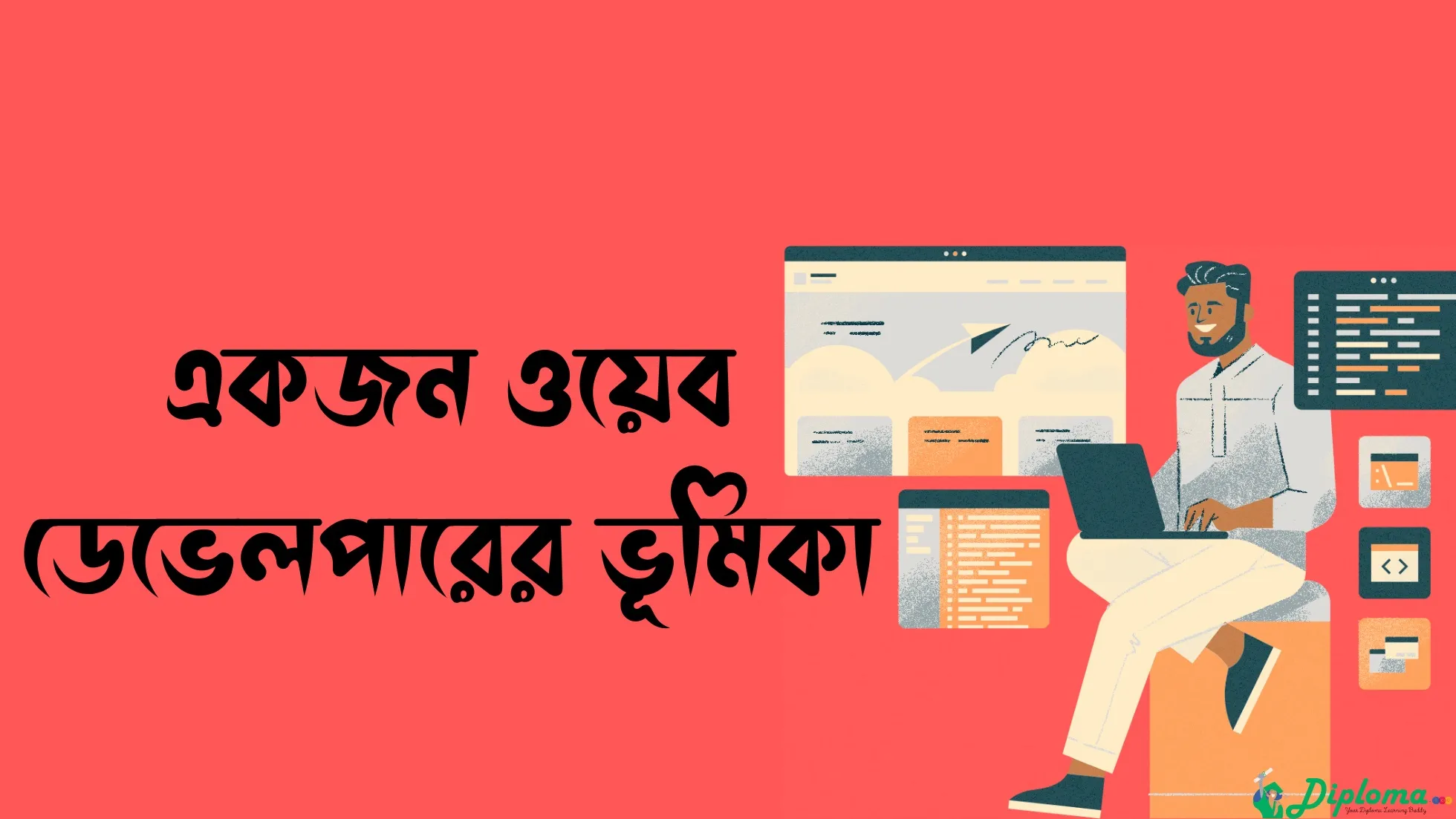
যে ব্যক্তি ওয়েব ডিজাইনারের তৈরি করা ওয়েবসাইট-কে প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে ডায়নামিক বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে রূপান্তর করে, তাকে ওয়েব ডেভেলপার বলে। মাঝে মাঝে ওয়েব ডেভেলপাররা ওয়েবসাইটের কিছু কিছু সেকশন তৈরিও করে থাকেন।
একজন ওয়েব ডেভেলপারের ভূমিকা তথা দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-
১। প্রোগ্রামিংঃ প্রোগ্রামিং করা একজন ওয়েব ডেভেলপারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভালো মানের ওয়েবসাইট তৈরির জন্য একজন ওয়েব ডেভেলপারকে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষার উপর দক্ষতা থাকতে হবে।
২। ডিজাইনারের সাথে আলোচনা: ওয়েবসাইট ডেভেলপ-এর পূর্বের ধাপ হলো ডিজাইন করা। একজন ডিজাইনার যখন ডিজাইন করেন, তখন ডিজাইনের জন্য ইনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন হয়। ওয়েব ডেভেলপার তার ওয়েবসাইটের ডেভেলপমেন্ট প্রসেস, ফিচার, সুযোগ-সুবিধা সবকিছু নিয়ে ডিজাইনারের সাথে আলোচনা করবে। অন্যথায় ডিজাইনারের তৈরিকৃত ডিজাইনগুলো বিফলে যাবে।
৩। পরিকল্পনা করাঃ কোনো কোনো ওয়েবসাইট তৈরির মূল প্ল্যানিং সিস্টেম অ্যানালিস্ট করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন ওয়েব ডেভেলপারকেও ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করতে হয়। এজন্য তাকে ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা করে সমস্ত চাহিদা বুঝে নিয়ে মূল পরিকল্পনা করতে হবে।
৪। ওয়েবসাইট ডিজাইন করা: সাধারণত একজন ওয়েব ডিজাইনার ওয়েবসাইট ডিজাইন করে থাকে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে ডেভেলপারকেও ডিজাইন করতে হয়। যে ডেভেলপাররা ডিজাইন ও ডেভেলপ উভয়ই পারে, তাদের চাহিদা বেশি এবং তারা বেশি পারিশ্রমিকে কাজ করতে পারেন। বা কোডে কোনোপ্রকার ভুল আছে কি না তা যাচাই করা একজন ওয়েব ডেভেলপারের অন্যতম কাজ। ওয়েবসাইটটি রিলিজ করার পূর্বে পুরো সিস্টেমকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করবে। এতে ভবিষ্যৎ জটিলতা কমবে।
৫। টেস্টিং: প্রোগ্রামিং এ ছাড়া ওয়েবসাইটটি লোড হতে কত সময় লাগছে, ব্যবহারকারী ওয়েবসাইটটি সহজে ব্যবহার করতে পারছে কি না, ওয়েবসাইটটি যেজন্য তৈরি করা হয়েছে সে চাহিদা পূরণ হচ্ছে কি না ইত্যাদি যাচাই করা একজন ওয়েব ডেভেলপারের কাজ। যদি কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে ওয়েব ডেভেলপার তা সমাধান করে দিবেন।
৬। ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ: ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ করা একজন ওয়েব ডেভেলপারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কনটেন্ট আপডেট করা, ওয়েবসাইটের কোড বিভিন্ন ব্রাউজারে সাপোর্ট করে কি না, ক্ষতিগ্রস্ত লিংক চেক করা, নতুন ইভেন্ট সংযোজন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া ওয়েবসাইটের মালিক যদি পুনরায় ডিজাইন বা পরিবর্তন করতে চান, তাহলে সেটা ওয়েব ডেভেলপারকে করে দিতে হবে।
৭। ডাটাবেস ম্যানেজারঃ ওয়েবসাইটগুলো যেহেতু অসংখ্য পরিমাণ ডাটা নিয়ে কাজ করে সেহেতু একজন ওয়েব ডেভেলপারকেও ডাটাবেস ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করতে হয়। ডাটাবেস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ব্যবহার না জানা থাকলে কখনোই ভালো মানের ওয়েব ডেভেলপার হওয়া যায় না।
AI & ইনফরমেশন টেকনোলজি
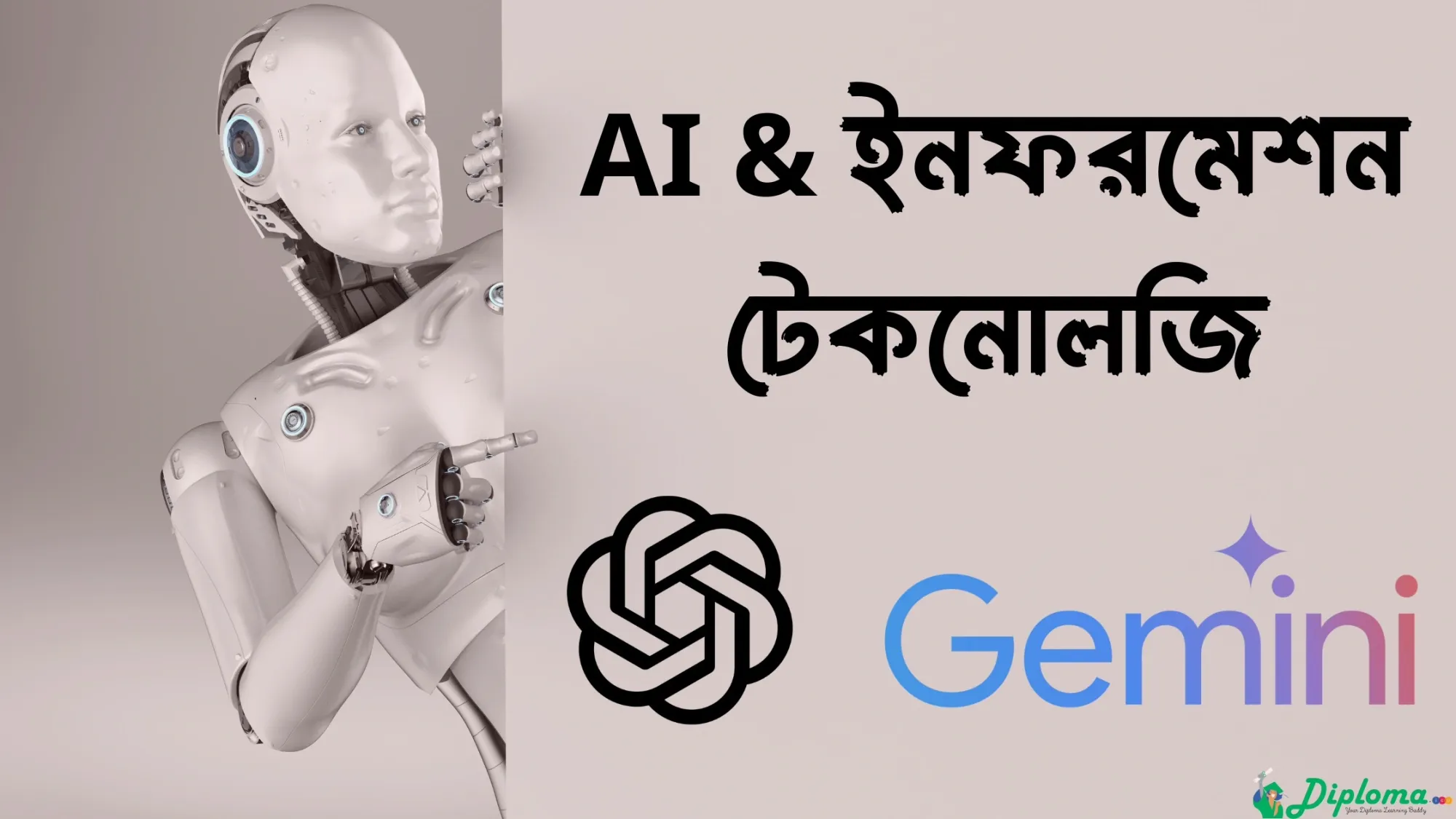
প্রতি বছর আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুনত্ব দেখা যায় এবং যে-কোনো পেশার মানুষদের জন্য এ নতুনত্ব বা ট্রেন্ডগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এ শিল্পে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ট্রেন্ডগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-
১। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial intelligence) : অটোমেশন প্রক্রিয়া বাড়ার সাথে সাথে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) দিনের আলোর মতো সবার চোখের সামনে চলে এসেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে এআই (AI) চালু হলেও ২০২৩ সালে এসে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ওয়েবসাইটভিত্তিক AI চালু হয়েছে, যেমন- ওয়েব এআই, ডিজাইন এআই ইত্যাদি। পরবর্তী বছরগুলোতে যার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
২। চ্যাটবটের উত্থান (Rise of chatbot) : চ্যাটবট হলো একটি প্রেগ্রাম, যা গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সমস্যা সমাধানের রাস্তা বলে দেয়। চ্যাটবট এখনো নিখুঁত সেবা না দিলেও মোটামুটি সেবা দিতে পারছে। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত Chat GPT ও Google Bard(Now Google Gemini ) উভয়ই Al চ্যাট বট।
৩। ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud computing)ঃ ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে এমন একটি কম্পিউটিং সিস্টেম যেখানে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক ডিভাইস প্রভৃতি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো সার্ভিস বা সেবা প্রদান করা হয়।
অন্যভাবে বলা যায়, ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেটভিত্তিক একটি কম্পিউটিং ব্যবস্থা, যেখানে কম্পিউটারের সমস্ত ডাটা ও সফটওয়্যার নিজের কম্পিউটারে না রেখে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাপস বা নেটওয়ার্কে জমা রাখা হয়।
৪। বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস (Big data analysis): বিগ ডাটা বলতে প্রতিদিনের নানারকমের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে সে বিপুল পরিমাণ ডাটা উৎপন্ন হয় তাকে বুঝায়। এ ধারণাটি বিগত কয়েক দশক ধরে চলে আসলেও বর্তমানে এর বিশালতা এত বেশি যে এটি পরিচালনা এবং বিশ্লেষণ করা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিগ ডাটাতে রয়েছে অসংখ্য মানুষের ব্যবহার, পছন্দ, যা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক লাভের পাশাপাশি আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে।
বিগ ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে ভালো ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে হাডুপ (Hadoop)। বিগ ডাটা অ্যানালাইটিক্সের জন্য হাডুপ ব্যবহার করছে অনেক বড় বড় কোম্পানি। চাকরিজীবীদের জন্য জনপ্রিয় সোশ্যাল ওয়েবসাইট লিঙ্কডইন (LinkedIn) হাডুপ ব্যবহার করে প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিলিয়নের বেশি চাকরির প্রস্তাবনা তৈরি করছে। ফলে লিঙ্কডইন ব্যবহারকারীরা শুধু তার পছন্দের সেক্টরের চাকরির প্রস্ত বিগুলোই দেখতে পায়।
৫। অটোমেশন (Automation): বর্তমানে অটোমেশন ট্রেন্ডের ব্যবহার খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অটোমেশন মানুষের জীবনযাত্রার মান সহজ করায় এর প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। যেমন-
- Automated parking system
- Automated school buses
- Metro rail
- Automated texting apps
- Robotic Gas pump
- Automated jewelry cleaning appliances
- Electronically automated doggy doors.
- Self-parking robot system
- Robotic barbecue cleaners
- Autonomous house ইত্যাদি।
৬। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual reality): ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বলতে বিভিন্ন ধরনের গেমিং অ্যাপস, নভোথিয়েটার, 3D শো ইত্যাদির ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে বুঝায়। এটির সাহায্যে ঘরে বসে বা থিয়েটারে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমন হবে তা কল্পনা করা যায়। বর্তমানে এটির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে।
৭। ব্লকচেইন ডাটা (Blockchain data): ব্লকচেইন (Blockchain) এক ধরনের চেইন বা শিকল। Block হচ্ছে ডাটা বা তথ্যের ব্লক। আর এ ব্লকগুলো যখন একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত হয়, তখন চেইনের মতো তৈরি হয়। তাই এটিকে ব্লকচেইন বলা হয়। ব্লকচেইন প্রযুক্তিতে অনেক ডাটা ব্লক থাকে।
এ সমস্ত ডাটা ব্লকে ক্রিপ্টোগ্রাফি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাটা এনকোড করা হয়। ব্লকচেইন হলো তথ্য রেকর্ডিং-এর এমন একটি ব্যবস্থা, যা সিস্টেমকে পরিবর্তন করা, হ্যাক করা বা প্রতারণা করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে।
৮। সাইবার সিকিউরিটি (Cyber security): বর্তমান উন্নত ইন্টারনেটের যুগে সাইবার সিকিউরিটি একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। যেখানে প্রতিনিয়ত গোপনীয় তথ্য চুরি বা আনঅথোরাইজড অ্যাক্সেস বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে তথ্যের নিরাপত্তা খুবই জরুরি। যার ফলে বড় বড় কোম্পানি বা সম্মানিত ব্যক্তিগণ সাইবার সিকিউরিটির দিকে ঝুঁকছে।
৯। আইওটি ডিভাইস (IoT Device): যখন একটি ডিভাইস তার প্রয়োজনে অন্য একটি ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত (Decision) গ্রহণ করতে পারে, তখন তাকে আইওটি ডিভাইস বলে। IoT ডিভাইসগুলো বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় এবং এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
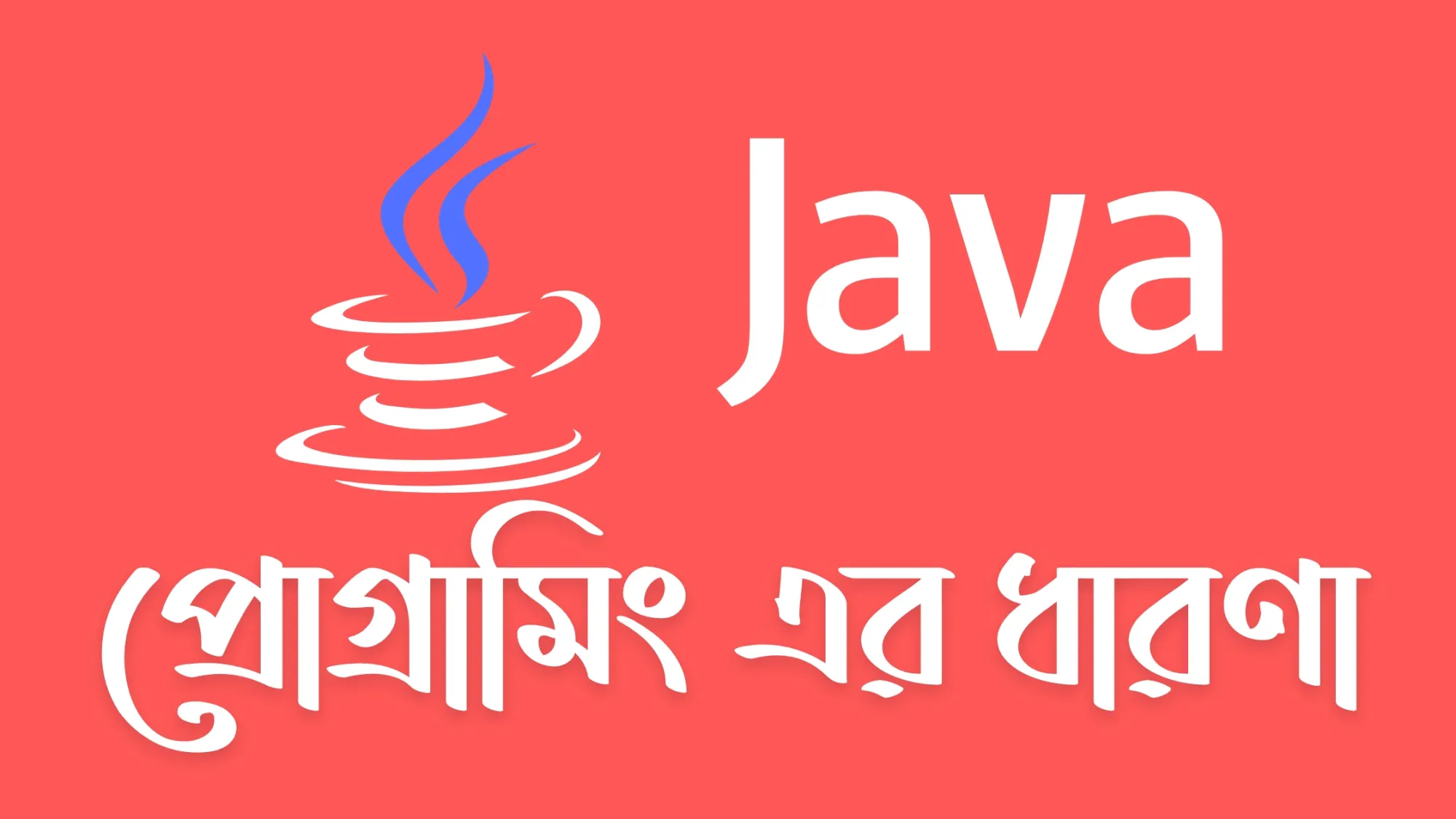
একজন ওয়েব ডেভেলপারের কর্মজীবনের সুযোগ
বর্তমানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটি জনপ্রিয় পেশা। এ পেশার উপর অনেকেই জীবিকানির্বাহ করছে। যে ব্যক্তি ওয়েবসাইট তৈরি বা ডেভেলপ করে, তাকে ওয়েব ডেভেলপার বলে। ওয়েব ডেভেলপারগণ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রথমে ডিজাইন বা চিত্র তৈরি করে এবং এরপর ক্লায়েন্ট সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ ও সার্ভার সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ওয়েবসাইট তৈরি বা ডেভেলপ করে থাকে।
দিন দিন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট- এর চাহিদা বাড়ায় একজন ওয়েব ডেভেলপারের কর্মসংস্থানও বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন ওয়েব ডেভেলপারের কর্মক্ষেত্রগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-
১। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি: ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিগুলো সাধারণত ওয়েবসাইট ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এখানে ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ড ও ফুল স্ট্যাক ডেভেলপারের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।
২। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিঃ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডেস্কটপ সফটওয়্যার তৈরি করে না, এরা ওয়েব সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশনও তৈরি করে। এ ছাড়া তাদের প্রডাক্ট ওয়েবসাইটে মার্কেটিং-এর জনাও অনেক ওয়েব ডেভেলপারের প্রয়োজন হয়।
৩। ফ্রিল্যান্সিংঃ ফ্রিল্যান্সিং বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় একটি পেশা। বর্তমানে ঘরে বসেই বিভিন্ন অলনাইন জব মার্কেট প্লেসে বা সরাসরি দেশের বাইরের ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছে বাংলাদেশের লাখ লাখ তরুণ-তরুণী। যার অধিকাংশ করছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ। ফলে এখানে কর্মসংস্থান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানঃ বর্তমানে সরকারি প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন ওয়েব ডেভেলপার বা প্রোগ্রামার পদে অনেক জনবল রয়েছে। আইসিটি-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার এ সেক্টরে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে সরকারি সেক্টরেও ওয়েব ডেভেলপারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫। প্রশিক্ষকঃ ওয়েব ডেভেলপারের চাহিদা পূরণের জন্য নতুনদের ওয়েব সম্পর্কে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। এজন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নেকটার, ভিটিটিআই ইত্যাদি এবং বিভিন্ন বেসরকারি ট্রেনিং সেন্টারে ওয়েব প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে এ নিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৬। বিভিন্ন সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান: আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি যেখানে ওয়েব ছাড়া কল্পনা করা যায় না। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব ডেভেলপারের প্রয়োজন হয়।
ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে W3C
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম (W3C) ১৯৯৪ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) এর উদ্ভাবক টিম বার্নাস-লি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যা ওয়েব প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক মানের নীতি প্রদান করে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম (W3C) ওয়েবসাইট তৈরির জন্য এক সেট নিয়ম বা স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করেছে, যেখানে এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট ইত্যাদির কোড লেখার নিয়ম, বিভিন্ন ফাইল ফরম্যাট, গোপনীয়তা এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
তবে তারা ওয়েবসাইটের অ্যাকচুয়াল ডিজাইনের উপর গুরুত্ব দেয় নি। ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড হলো মার্কেটার ও ওয়েব ডিজাইনারের বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে তৈরি করা ওয়েবপেজ লেআউট ও ইউএক্স ফিচার। ডিজাইন যেমনই হোক না কেন কোডিং স্টাইলে বা লেআউটে যেন কোনো ভুল না থাকে।
ওয়েবসাইট তৈরি করার পর W3C ভ্যালিডেটর থেকে কোড ভ্যালিডেশন করা যাবে। এখানে সরাসরি কোডিং দিয়ে বা কোডিং ফাইল আপলোড করে অথবা ওয়েবসাইট হোস্ট করার পর ডোমেইন নেম দিয়েও কোড ভ্যালিড কি না যাচাই করা যায়। কোডে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে কতগুলো ভুল আছে এবং কোথায় ভুল আছে, সেটি নির্দেশ করে।
W3C ওয়েব ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলার কারণ:
পূর্বে যখন ইন্টারনেটের বিকাশ শুরু হয়, তখন ওয়েবপেজ ডিজাইন, ব্রাউজার সামঞ্জস্যতা ইত্যাদির কোনো সট্যান্ডার্ড নিয়ম ছিল না। ফলে অনেক কোড ব্রাউজারে কাজ করত না এবং ওয়েবসাইটগুলো অনেক কম গতির ছিল। এ ছাড়া ওয়েবসাইটগুলোকে সকল বাক্তি সমানভাবে অ্যাক্সেস করতে পারত না। এতে ওয়েবসাইট তৈরির উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে পড়ত।
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম (W3C)-এর একটি নির্দিষ্ট মিশন ছিল ওয়েবকে তার চূড়ান্ত সম্ভাবনায় নিয়ে আসা। এবং একটি সুমিনিয় নিয়ম তৈরি করে দিয়েছে, যা অনুসরণ করাল সকল ওয়েবসাইট একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড-এ চলে আসবে।
ইউআরএল সম্পর্কে বর্ণনা

URL-এর পূর্ণরূপ হলো Uniform Resource Locator কোনো একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কে না ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার জন্য একটি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়। এ অ্যাড্রেস বা ওয়েব আড্রেসকেই URL বলা হয়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি URI. হলো কোনো নেটওয়ার্ক বা ওয়েবসাইটের ইউনিক আইডেন্টিটি বা ঠিকানা। যেমন-
সাধারণত একটি URL-এর ৩টি অংশ থাকে; যথা-
- প্রটোকল (Protocol)
- ডোমেইন (Domain)
- পাথ (Path) |
প্রটোকল (Protocol)
একটি URL-এর প্রথম অংশ প্রাথমিক অ্যাক্সেস মাধ্যম হিসেবে কোন প্রটোকল ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে। URL প্রটোকলের মধ্যে রয়েছে HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), Mailto, FTP, Telnet ইত্যাদি।
HTTP বা HTTPS: ওয়েব অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে আমরা HTTP বা HTTPS উভয়ই দেখতে পাই। HTTPS থাকলে বুঝতে হবে উক্ত ওয়েবসাইটে SSL ইনস্টল করা আছে এবং ডাটা সুরক্ষিত আছে। SSL হলো Secure Sockets Layer, যা ক্লায়েন্ট কম্পিউটার ও ওয়েব সার্ভারের মধ্যে যোগাযোগের সময় ডাটা এনক্রিপ্ট করে গোপনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।
Mailto: Mailto হলো ই-মেইল প্রটোকল যার সাহায্যে ই-মেইল পাঠানো যায়।
FTP : FTP হলো File Transfer Protocol। এ প্রটোকল দ্বারা URL-এর সাহায্যে কোনো একটি FTP সার্ভারের ফাইল অ্যাক্সেস করা যায়।
Telnet: Telnet হলো একটি সিস্টেমের সাথে অন্য একটি সিস্টেম যুক্ত হবার প্রটোকল। এটি সাধারণত রিমোট লগিন-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এখানে কোনো ব্যাক্তি তার কম্পিউটারকে দূরবর্তী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করে এবং দূরবর্তী কম্পিউটার অনুরোধ গ্রহণ করে সংযোগ স্থাপন করে।
ডোমেইন (Domain)

উদাহরণে দেয়া bangladesh হলো ইউনিক ডোমেইন, gov হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য টপ লেভেল ডোমেইন এবং bd হলো দেশের নাম। আমরা যদি আরো কিছু উদাহরণ দেখি যেমন- bangladesh.gov.bd, google.com, wordpress.org তাহলে বুঝতে পারছি যে সবার শেষে.com, .org, .edu রয়েছে। এ .com, .org, .edu ইত্যাদিকে TOP level domain (TLD) বলা হয়।
মূল ডোমেইন নামের শুরুতে যদি কোনো অতিরিক্ত অংশ থাকে তাহলে তাকে Sub-domain বলে। যেমন- hey.google.com ইত্যাদি। সাব ডোমেইনকেও আমরা ডোমেইন হিসেবে বিবেচনা করব।
পাথ (Path)
ডোমেইন নেমের পরের অংশ হলো পাথ (Path)। এখানে Path হিসেবে ‘Notice’ রয়েছে অর্থাৎ এটি হলো ডকুমেন্টের নাম। Path হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পেজ বা ফাইলকে নির্দেশ করে যা উক্ত ওয়েবসাইটেই রয়েছে। এখানে যদি আমরা URL হিসেবে Notice লিখি তাহলে উক্ত ওয়েবসাইটের Notice পেজ দেখতে পাব।
URL যেভাবে কাজ করে
কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সফটওয়্যার কোনো ডোমেইন নেমকে বুঝতে পারে না। এটি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বা আইপি অ্যাড্রেস বুঝে। তাই প্রত্যেক ডোমেইন নেমের সাথে একটি IP address যুক্ত করা হয়।
ডোমেইন নেম ব্যবহার না করে শুধুমাত্র IP address দিয়েও সরাসরি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যায়। Domain name বা URL-কে IP address-এ পরিনত করার জন্য আমাদের ব্রাউজারগুলো Domain Name Server (DNS) নামে একটি পরিষেবা ব্যবহার করে থাকে।



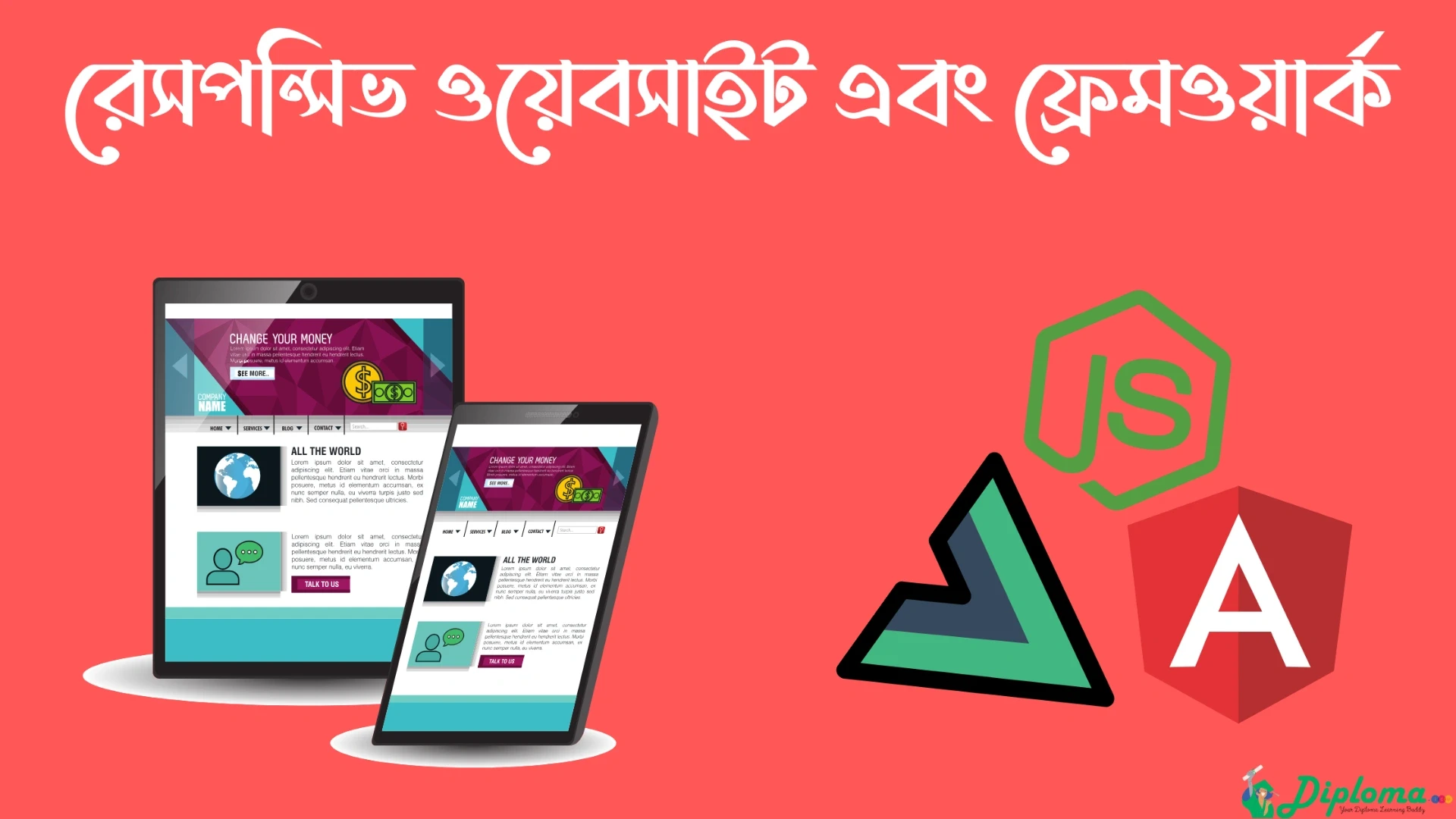



Thanks to All 🙂
খুব ভালো লিখেছেন এই আর্টিকেলটি। ওয়েব প্রযুক্তি নিয়ে এত বিশদ আলোচনা বেশ তথ্যবহুল। একটা প্রশ্ন ছিলো—ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কোন টুল বা ফ্রেমওয়ার্ক সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করেন?
হালকা তথ্য শেয়ার করতে চাইলে এই ব্লগ পেজটি দেখতে পারেন, https://sebbie.pl/tag/java/ – যেখানে বিভিন্ন প্রযুক্তির আলোচনা আছে।
ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে টুল বা ফ্রেমওয়ার্ক বেছে নেওয়ার আগে আপনার প্রয়োজন এবং প্রকল্পের ধরন বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
খুবই উপকারী এবং তথ্যপূর্ণ পোস্ট। ধন্যবাদ!
বেশ ভালো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পোস্টটি সাজানো হয়েছে! ওয়েব টেকনোলজি, ফ্রন্ট-এন্ড, ব্যাক-এন্ড এবং ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে AI, ক্লাউড কম্পিউটিং, এবং সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে বর্তমান ট্রেন্ডগুলো জেনে উপকৃত হলাম। ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে জেনে অনেক ভালো লাগল। শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট।